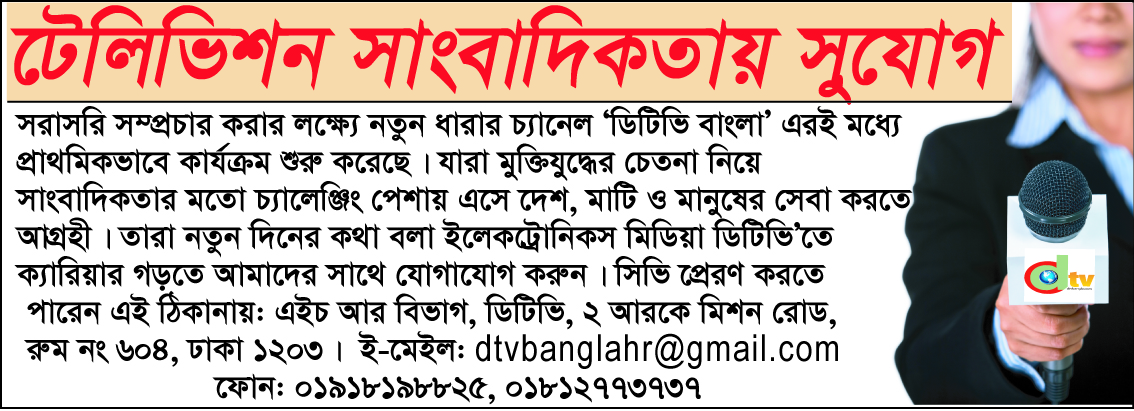ভারতের চিনি রপ্তানিতে লাগাম, দেশে চাপ বাড়বে কি?
ব্রাজিলের পর বিশ্বে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ চিনি রপ্তানিকারক দেশ ভারত। আর বাংলাদেশের জন্য পণ্যটি তৃতীয় বৃহত্তম আমদানির উৎস। এখন ভারত নিজ দেশের অভ্যন্তরে দামের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে চিনি রপ্তানি সীমিত করার পরিকল্পনা করছে। যার প্রভাব বাংলাদেশের বাজারেও পড়তে পারে বলে আশঙ্কা ব্যবসায়ীদের। যদিও সরকার তেমনটি মনে করছে না। মঙ্গলবার (২৫ মে) ভারতের একটি সরকারি সূত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, দেশটি চলতি মৌসুমে চিনির রপ্তানি এক কোটি টনে সীমাবদ্ধ করতে পারে। কারণ, সরকারি ভর্তুকি ছাড়া ভারতীয় কারখানাগুলো চলতি ২০২১-২২ বিপণনবর্ষে এ পর্যন্ত ৮৫ লাখ টন চিনি রপ্তানির চুক্তি করে ফেলেছে। এরইমধ্যে প্রায় ৭১ লাখ টন চিনি বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে তারা। সেজন্য নিজেদের বাজার স্থিতিশীল রাখতে এ সিদ্ধান্ত আসছে। যদিও কবে থেকে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হবে সে বিষয়টি এখনো পরিষ্কার করা হয়নি। তবে আগামী মাসের শুরু থেকেই দেশটি চিনি রপ্তানিতে লাগাম টানতে পারে বলে জানিয়েছে ভারতের ওই সরকারি সূত্র। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা বলছেন, ভারতীয় চিনি রপ্তানি সীমিত হলে বিশ্ববাজারে পণ্যটির দাম বেড়ে যেতে পারে। পাশাপাশি বাংলাদেশের মতো অন্যান্য আমদানিকারক দেশগুলো বিকল্প উৎসের ওপর চাহিদা বাড়াবে। তাতে ব্রাজিল, যুক্তরাজ্য ও চীনের মতো রপ্তানিকারক দেশগুলোর বাজারেও সরবরাহের টান পড়তে পারে। যা নিশ্চিতভাবেই দুশ্চিন্তার কারণ। নাম প্রকাশ না করার শর্তে দেশের অন্যতম আমদানিকারক শিল্প গ্রুপের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা জাগো নিউজকে বলেন, ‘আগে ভারত থেকে তুলনামূলক চিনি আমদানি কম হলেও করোনা মহামারির সময় থেকে তা বেড়েছে। কারণ, অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় ভারত থেকে পরিবহন খরচ কম। ফলে এখন ভারতীয় চিনি চাহিদা মতো না পেলে দেশের বাজারে অবশ্যই প্রভাব পড়বে। এটা সাধারণ বিষয়।’তবে ওই কর্মকর্তার ভাষ্য, ‘এ ধরনের পরিস্থিতি কিছুটা সময়সাপেক্ষ। এখনো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না যে বাংলাদেশ কী পরিমাণ চিনি আনতে পারবে বা পারবে না। কারণ, ভারত কিন্তু এখনো রপ্তানি বন্ধ বা সীমিত করেনি। এমনও হতে পারে প্রতিবেশী দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে চাহিদা অনুয়ায়ী পণ্যটির সরবরাহ অব্যাহত রাখা হবে।’বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি চিনি আমদানি করে ব্রাজিল থেকে। এরপর চীন এবং ভারত। এছাড়াও যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ও মালয়েশিয়া থেকেও আসে অপরিশোধিত চিনি। ফলে বিশ্ববাজারে ভারত রপ্তানি সীমিত করলেও বাংলাদেশে এর প্রভাব খুব একটা পড়বে না বলে মনে করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। সংস্থাটির আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (আইআইটি) অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব এ কে এম আলী আহাদ খান জাগো নিউজকে বলেন, চিনির জন্য আমরা ভারতের ওপর ততোটা নির্ভরশীল নই। ভারত রপ্তানি সীমিত করলেও বিকল্প অনেক দেশ রয়েছে। সেজন্য চিন্তার কোনো কারণ নেই। সমস্যা হবে না। এক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ বা প্রস্তুতি আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখনো ভারতের পক্ষ থেকে অফিসিয়ালি কিছু জানতে পারিনি। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন হলে যে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তথ্য বলছে, দেশে চিনির চাহিদার প্রায় পুরোটাই এখন আমদানিনির্ভর। রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলোতে যে পরিমাণ চিনি উৎপাদন হয় সেটা চাহিদার তুলনায় খুবই নগণ্য। বিগত পাঁচ বছরে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আমদানি হয়েছে এক কোটি সাড়ে ১১ লাখ টনের বেশি অপরিশোধিত চিনি। দেশের বৃহৎ পাঁচটি শিল্প গ্রুপ এসব চিনির আমদানিকারক। এরমধ্যে সিংহভাগ চিনি আমদানি করেছে সিটি ও মেঘনা গ্রুপ। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এরপরই তালিকায় আছে এস আলম, আবদুল মোনেম লিমিটেড ও দেশবন্ধু সুগার মিল। দেশে বছরে কমবেশি ২০ থেকে ২২ লাখ টন পরিশোধিত চিনির চাহিদা রয়েছে। এরমধ্যে রাষ্ট্রীয় চিনিকলগুলো চাহিদার ন্যূনতমও পূরণ করতে পারছে না। দেশীয় চিনির উৎপাদন কমতে কমতে তা এখন সর্বনিম্ন স্তরে নেমেছে। যেখানে এক দশক আগেও (২০১২-১৩ অর্থবছর) দেশের চিনিকলগুলোর বার্ষিক উৎপাদন ছিল এক লাখ টনের উপরে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৫টি রাষ্ট্রীয় চিনিকলে প্রায় ৮২ হাজার টন উৎপাদন হয়েছিল। ২০২০ সালের শেষ দিকে ছয়টি চিনিকল বন্ধের ঘোষণা আসার পর গত আখ মাড়াই মৌসুমে (২০২০-২১ অর্থবছর) উৎপাদন কমে দাঁড়ায় ৪৮ হাজার ১৩৩ টনে। সবশেষ চলতি মৌসুমে (২০২১-২২ অর্থবছর) উৎপাদন আরও কমে নামে ২৪ হাজার ৯শ টনে।দেশে চিনি উৎপাদনের এই ক্রম নিম্নমুখী ধারার প্রেক্ষাপটে দিন দিনই বাড়ছে আমদানি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে পাওয়া তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২১ লাখ ৬১ হাজার ৯৭২ টন, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২২ লাখ ৯৫ হাজার ৯৮৮ টন,
২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২২ লাখ ৩৮ হাজার ৮২৯ টন, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২১ লাখ ৭০ হাজার ১৬৮ টন এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে আমদানি হয়েছে ২২ লাখ ৮৫ হাজার ৬০৩ টন অপরিশোধিত চিনি। অন্যদিকে ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, গত বছর দেশটি ২ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলারের চিনি রপ্তানি করছে। এরমধ্যে বাংলাদেশ দ্বিতীয় সবোর্চ্চ ক্রেতা। ভারত সবচেয়ে বেশি চিনি রপ্তানি করেছে ইন্দোনেশিয়ায় ৭৬৯ মিলিয়ন ডলারের। এরপর বাংলাদেশে ৫৬১ মিলিয়ন ডলারের। এছাড়া সুদান ও সংযুক্ত আবর আমিরাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে চিনি রপ্তানি করেছে প্রতিবেশী দেশটি। ২০১৬ সালে ভারত চিনি রপ্তানির ওপর ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপের পর বিগত বছরগুলোতে এ পণ্যের রপ্তানিতে কোনো নিষেধাজ্ঞা দেয়নি। অর্থাৎ, টানা ছয় বছর বিশ্বব্যাপী চিনির বড় উৎস হিসেবে কাজ করেছে দেশটি। কিন্তু গত দুই বছরে ১৪ মিলিয়ন টনেরও বেশি রপ্তানির পর ভারত সরকার অগ্রাধিকারভিত্তিতে স্থানীয় চাহিদা মেটাতে চিনি উৎপাদনের ওপর নজর দিয়েছে।
|

ব্রাজিলের পর বিশ্বে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ চিনি রপ্তানিকারক দেশ ভারত। আর বাংলাদেশের জন্য পণ্যটি তৃতীয় বৃহত্তম আমদানির উৎস। এখন ভারত নিজ দেশের অভ্যন্তরে দামের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে চিনি রপ্তানি সীমিত করার পরিকল্পনা করছে। যার প্রভাব বাংলাদেশের বাজারেও পড়তে পারে বলে আশঙ্কা ব্যবসায়ীদের। যদিও সরকার তেমনটি মনে করছে না। মঙ্গলবার (২৫ মে) ভারতের একটি সরকারি সূত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, দেশটি চলতি মৌসুমে চিনির রপ্তানি এক কোটি টনে সীমাবদ্ধ করতে পারে। কারণ, সরকারি ভর্তুকি ছাড়া ভারতীয় কারখানাগুলো চলতি ২০২১-২২ বিপণনবর্ষে এ পর্যন্ত ৮৫ লাখ টন চিনি রপ্তানির চুক্তি করে ফেলেছে। এরইমধ্যে প্রায় ৭১ লাখ টন চিনি বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে তারা। সেজন্য নিজেদের বাজার স্থিতিশীল রাখতে এ সিদ্ধান্ত আসছে। যদিও কবে থেকে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হবে সে বিষয়টি এখনো পরিষ্কার করা হয়নি। তবে আগামী মাসের শুরু থেকেই দেশটি চিনি রপ্তানিতে লাগাম টানতে পারে বলে জানিয়েছে ভারতের ওই সরকারি সূত্র। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা বলছেন, ভারতীয় চিনি রপ্তানি সীমিত হলে বিশ্ববাজারে পণ্যটির দাম বেড়ে যেতে পারে। পাশাপাশি বাংলাদেশের মতো অন্যান্য আমদানিকারক দেশগুলো বিকল্প উৎসের ওপর চাহিদা বাড়াবে। তাতে ব্রাজিল, যুক্তরাজ্য ও চীনের মতো রপ্তানিকারক দেশগুলোর বাজারেও সরবরাহের টান পড়তে পারে। যা নিশ্চিতভাবেই দুশ্চিন্তার কারণ। নাম প্রকাশ না করার শর্তে দেশের অন্যতম আমদানিকারক শিল্প গ্রুপের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা জাগো নিউজকে বলেন, ‘আগে ভারত থেকে তুলনামূলক চিনি আমদানি কম হলেও করোনা মহামারির সময় থেকে তা বেড়েছে। কারণ, অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় ভারত থেকে পরিবহন খরচ কম। ফলে এখন ভারতীয় চিনি চাহিদা মতো না পেলে দেশের বাজারে অবশ্যই প্রভাব পড়বে। এটা সাধারণ বিষয়।’তবে ওই কর্মকর্তার ভাষ্য, ‘এ ধরনের পরিস্থিতি কিছুটা সময়সাপেক্ষ। এখনো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না যে বাংলাদেশ কী পরিমাণ চিনি আনতে পারবে বা পারবে না। কারণ, ভারত কিন্তু এখনো রপ্তানি বন্ধ বা সীমিত করেনি। এমনও হতে পারে প্রতিবেশী দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে চাহিদা অনুয়ায়ী পণ্যটির সরবরাহ অব্যাহত রাখা হবে।’বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি চিনি আমদানি করে ব্রাজিল থেকে। এরপর চীন এবং ভারত। এছাড়াও যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ও মালয়েশিয়া থেকেও আসে অপরিশোধিত চিনি। ফলে বিশ্ববাজারে ভারত রপ্তানি সীমিত করলেও বাংলাদেশে এর প্রভাব খুব একটা পড়বে না বলে মনে করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। সংস্থাটির আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (আইআইটি) অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব এ কে এম আলী আহাদ খান জাগো নিউজকে বলেন, চিনির জন্য আমরা ভারতের ওপর ততোটা নির্ভরশীল নই। ভারত রপ্তানি সীমিত করলেও বিকল্প অনেক দেশ রয়েছে। সেজন্য চিন্তার কোনো কারণ নেই। সমস্যা হবে না। এক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ বা প্রস্তুতি আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখনো ভারতের পক্ষ থেকে অফিসিয়ালি কিছু জানতে পারিনি। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন হলে যে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তথ্য বলছে, দেশে চিনির চাহিদার প্রায় পুরোটাই এখন আমদানিনির্ভর। রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলোতে যে পরিমাণ চিনি উৎপাদন হয় সেটা চাহিদার তুলনায় খুবই নগণ্য। বিগত পাঁচ বছরে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আমদানি হয়েছে এক কোটি সাড়ে ১১ লাখ টনের বেশি অপরিশোধিত চিনি। দেশের বৃহৎ পাঁচটি শিল্প গ্রুপ এসব চিনির আমদানিকারক। এরমধ্যে সিংহভাগ চিনি আমদানি করেছে সিটি ও মেঘনা গ্রুপ। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এরপরই তালিকায় আছে এস আলম, আবদুল মোনেম লিমিটেড ও দেশবন্ধু সুগার মিল। দেশে বছরে কমবেশি ২০ থেকে ২২ লাখ টন পরিশোধিত চিনির চাহিদা রয়েছে। এরমধ্যে রাষ্ট্রীয় চিনিকলগুলো চাহিদার ন্যূনতমও পূরণ করতে পারছে না। দেশীয় চিনির উৎপাদন কমতে কমতে তা এখন সর্বনিম্ন স্তরে নেমেছে। যেখানে এক দশক আগেও (২০১২-১৩ অর্থবছর) দেশের চিনিকলগুলোর বার্ষিক উৎপাদন ছিল এক লাখ টনের উপরে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৫টি রাষ্ট্রীয় চিনিকলে প্রায় ৮২ হাজার টন উৎপাদন হয়েছিল। ২০২০ সালের শেষ দিকে ছয়টি চিনিকল বন্ধের ঘোষণা আসার পর গত আখ মাড়াই মৌসুমে (২০২০-২১ অর্থবছর) উৎপাদন কমে দাঁড়ায় ৪৮ হাজার ১৩৩ টনে। সবশেষ চলতি মৌসুমে (২০২১-২২ অর্থবছর) উৎপাদন আরও কমে নামে ২৪ হাজার ৯শ টনে।দেশে চিনি উৎপাদনের এই ক্রম নিম্নমুখী ধারার প্রেক্ষাপটে দিন দিনই বাড়ছে আমদানি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে পাওয়া তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২১ লাখ ৬১ হাজার ৯৭২ টন, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২২ লাখ ৯৫ হাজার ৯৮৮ টন,
২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২২ লাখ ৩৮ হাজার ৮২৯ টন, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২১ লাখ ৭০ হাজার ১৬৮ টন এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে আমদানি হয়েছে ২২ লাখ ৮৫ হাজার ৬০৩ টন অপরিশোধিত চিনি। অন্যদিকে ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, গত বছর দেশটি ২ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলারের চিনি রপ্তানি করছে। এরমধ্যে বাংলাদেশ দ্বিতীয় সবোর্চ্চ ক্রেতা। ভারত সবচেয়ে বেশি চিনি রপ্তানি করেছে ইন্দোনেশিয়ায় ৭৬৯ মিলিয়ন ডলারের। এরপর বাংলাদেশে ৫৬১ মিলিয়ন ডলারের। এছাড়া সুদান ও সংযুক্ত আবর আমিরাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে চিনি রপ্তানি করেছে প্রতিবেশী দেশটি। ২০১৬ সালে ভারত চিনি রপ্তানির ওপর ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপের পর বিগত বছরগুলোতে এ পণ্যের রপ্তানিতে কোনো নিষেধাজ্ঞা দেয়নি। অর্থাৎ, টানা ছয় বছর বিশ্বব্যাপী চিনির বড় উৎস হিসেবে কাজ করেছে দেশটি। কিন্তু গত দুই বছরে ১৪ মিলিয়ন টনেরও বেশি রপ্তানির পর ভারত সরকার অগ্রাধিকারভিত্তিতে স্থানীয় চাহিদা মেটাতে চিনি উৎপাদনের ওপর নজর দিয়েছে।
|
|
|
|

ঢাকা: নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়াতে খাদ্যদ্রব্যসহ অর্থনীতিতে যে বৈশ্বিক সংকটের আশঙ্কা করা হচ্ছে বাংলাদেশে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না বলে মনে করছেন সরকার ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকরা। এ সংক্রান্ত যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে সরকার আগে থেকেই সতর্ক অবস্থান নিয়েছে বলে জানিয়েছেন তারা। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে সারা বিশ্বে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়তে থাকা এবং অর্থনীতির ওপর এর নেতিবাচক প্রভাবের আশঙ্কা করা হচ্ছে। খাদ্যপণ্যসহ অন্যন্যা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দামের ঊর্ধ্বগতিও এরই মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পরিস্থিতির পর্যালোচনায় বিশেষজ্ঞরা খাদ্য সংকট তৈরির আশঙ্কা করছেন এবং এ বিষয়ে তারা সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিচ্ছেন। গত ১৯ মে বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, জাতিসংঘ সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, সামনের মাসগুলোতে বৈশ্বিক খাদ্য সংকট তৈরি হতে পারে। সংস্থাটির মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, এই যুদ্ধের (ইউক্রেন-রাশিয়া) কারণে দাম বাড়ায় দরিদ্র দেশগুলোতে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ভয়াবহ পর্যায়ে চলে গেছে। তার আশঙ্কা, শেষ পর্যন্ত ইউক্রেন থেকে রপ্তানি স্বাভাবিক না হলে বিশ্ব দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হতে পারে। খাদ্য সংকটের কারণে কোটি কোটি মানুষ অপুষ্টি, ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের মুখে পড়তে পারে। ইউক্রেনের খাদ্যশস্য স্বাভাবিক পর্যায়ে আনা ছাড়া খাদ্য সংকটের কার্যকর কোনো সমাধান নেই। একই ভাবে বৈশ্বিক বাজারে রাশিয়া ও বেলারুশের সারেরও বিকল্প নেই। এদিকে বাংলাদেশে এর প্রভাব সম্পর্কে সরকারের সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, সম্প্রতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়তে থাকায় সরকারের নীতিনির্ধারকরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। বৈশ্বিক সংকটের প্রভাব বাংলাদেশেও পড়তে পারে এ আশঙ্কা থেকে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো তৎপরতা শুরু করেছে। এই সংকটের প্রভাব যাতে না পড়ে সে জন্য করণীয় কী হবে- সে বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে এ ব্যাপারে জরুরি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়া এবং ডলার সংকট মোকাবিলাসহ বাজার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে অর্থ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট দফতরগুলোকে জরুরি সমন্বয় বৈঠকের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত ১৯ মে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশ দিয়েছেন বলে বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব। গত রোববার (২২ মে) এক অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ বৈশ্বিক সংকটের প্রভাব বাংলাদেশেও পড়তে পারে বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে সারা বিশ্বে যে প্রভাব পড়েছে তার থেকে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন না। বাংলাদেশেও এর প্রভাব বিস্তার করবে তার আলামত আমরা কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছি। যদিও সরকার ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকরা বাংলাদেশে এর বড় ধরনের প্রভাব পড়বে না বলে আশা করছেন। বাংলাদেশের খাদ্য ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যে পর্যায়ে রয়েছে তাতে এ ধরনের কোনো সংকট তৈরি বা সমস্যা হবে না। তাছাড়া সংকট মোকাবিলায় আগে থেকেই সরকার করণীয় নির্ধারণে সচেষ্ট আছে বলে জানান তারা। জাতিসংঘ থেকেও বৈশ্বিক খাদ্য সংকটের আশঙ্কা করা হচ্ছে, বাংলাদেশে এর প্রভাব পড়ার কোনো আশঙ্কা আছে কি-না জানতে চাইলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বাংলানিউজকে বলেন, না, আমরা এখনও অনেক ভালো অবস্থানে আছি। কোনো সমস্যা হবে না বলে মনে করি। আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলানিউজকে তিনি বলেন, সারা পৃথিবীতেই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। সরকার চেষ্টা করছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে চেষ্টা করছেন সেভাবে চললে সাধারণ মানুষের গায়ে তাপ লাগবে না বলে আশা করি। এ বিষয়ে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বাংলানিউজকে বলেন, আমরাতো বিশ্বের মধ্যেই আছি। সারা পৃথিবীতে যেটার প্রভাব পড়বে, সেটা তো এখানেও পড়তে পারে। করোনোয় সারা বিশ্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা তো এর বাইরে না। তবে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছি পরিস্থিতি যাতে স্বাভাবিক থাকে, জনগণ যাতে ভোগান্তিতে না পড়ে। সোমবার(২৩ মে) এক অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার জানিয়েছেন, বাংলাদেশে খাদ্যের জন্য হাহাকার হবে না। সারা বিশ্বে যখন খাদ্যের দাম বাড়ে তখন এখানেও (বাংলাদেশে) খাদ্যের দাম বাড়তে পারে। তবে দেশে প্রচুর খাদ্য মজুদ আছে। সামনে আউশ চাষাবাদ হবে, আশা করা যায়, উৎপাদনও ভালো হবে।
|
|
|
|

খাদ্য নিরাপত্তায় বিশেষ অবদানের জন্য এ বছর স্বাধীনতা পদক পেয়েছেন ড. মো. আব্দুল মজিদ। তার উদ্ভাবিত ধানের স্বল্প সময়ে উৎপাদন পদ্ধতি বরেন্দ্র অঞ্চলে মঙ্গা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পাশাপাশি অন্যান্য শস্যের বহুমুখিকরণে নিরলস গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।
ধান চাষে সবচেয়ে কম সময়ে উল্লেখযোগ্য নতুন প্রযুক্তি বরেন্দ্র এলাকার শুষ্ক জমিতে চারা রোপন না করে সরাসরি ধান বপন ও অন্যান্য শস্য বিন্যাসের প্রযুক্তির উদ্ভাবন। যা বিরিধান-৩৩ নামে পরিচিত।
কম সময়ে এই ধান উৎপাদন পদ্ধতির আবিষ্কার ড. মো. আব্দুল মজিদ। জিনি খাদ্য নিরাপত্তায় বিশেষ অবদানের জন্য এ বছর স্বাধীনতা পদক পেয়েছেন।
এই উদ্ভাবনের ফলে কম সময়ে কৃষকেরা ধান ঘরে তুলতে পারেন। পাশাপাশি একই জমিতে তিনটি ফসল উৎপাদনও সম্ভব হচ্ছে।
ধানের স্বল্প জীবনকাল জাতের উৎপাদন পদ্ধতির আকিষ্কারক ড. মো. আব্দুল মজিদ বলেছেন, ধান যাতে অল্প সময়ের মধ্যে কাটা যায়, যাতে করে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। তার সাথে ঐ জমিটি আগাম খালি হয়ে যাচ্ছে তাতে করে অন্যান্য ফসলও আবাদে শস্য নিবিরতা ও শস্য বহুমুখিকরণই আবিষ্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল।
তার মতে, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ধরে রাখতে নতুন জাতের ধানের উৎপাদন বাড়ানোসহ কৃষকদের মাঝে পরিচিতি তুলে ধরতে হবে। এজন্য ভিডিও বেজড টেকনোলজির কথাও উল্লেখ করেন তিনি
বন্যা সহিষ্ণু জাত উৎপাদন ও মানুষের পুষ্টি চাহিদা রমটাতে নতুন জাতের উৎপাদন পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছেন তিনি।
|
|
|
|

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ বলেছেন, পাশের বাসায় অভাবী লোক রেখে আপনিও নিরাপদ থাকতে পারবেন না।
মঙ্গলবার (২৭ মার্চ) রাজধানীর খামার বাড়ির আ. কা. মু. গিয়াস উদ্দীন মিলকী অডিটরিয়ামে ‘এসডিজি’( টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য) বাস্তবায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভূামিকা ও করণীয়’ শীর্ষক দিনব্যাপি সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ সেমিনার আয়োজন করে।
এসডিজি অর্জনে তাগিদ দিয়ে সিনিয়র সচিব বলেন, কাউকে পিছিয়ে রেখে উন্নয়নকে টেকসই করা যাবে না। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতের জন্য সকলকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।
তিনি বলেন, এসডিজির লক্ষ্য অনুযায়ী সমাজের সব ধরনের দারিদ্র্য বিলোপ এবং ক্ষুধা মুক্তির জন্য দেশের খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুন করতে হবে। এজন্য কৃষির সম্প্রসারণ ও গবেষণার কাজকে উন্নত এবং গতিশীল করতে হবে। সরকারের কার্যকর উদ্যোগে মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল বাস্তবায়নের সাফল্যে ৪৭ বছরে বাংলাদেশে ধান উৎপাদন বেড়েছে তিনগুন এবং শাকসবজি ও ফলের উৎপাদন বেড়েছে দ্বিগুন।
কৃষকের তামাক চাষের বিষয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে সিনিয়র সচিব মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ বলেন, বাংলাদেশের কৃষক স্বাধীন। সরকার কৃষকের স্বাধীনতা হরন করতে পারে না এবং করেওনি। কৃষকের দায় পড়েনি ক্রমাগত লোকসান দিয়ে ধান চাষ করবে। বিকল্প না দিয়ে কৃষককে তামাক চাষ না করার জন্য বাধ্য করা যাবে না। তামাক চাষ সরকার ব্যান্ডও করেনি। তামাক চাষের জন্য সরকার কোনো রকমের সহায়তা ও উৎসাহ দিচ্ছে না। বরং তামাক চাষ কমাতে সরকার নানা প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। এতে দেশে তামাক চাষ কমে আসেছে।
সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহা পরিচালক মোহাম্মদ মহসীন। সমাগত বক্তব্য দেন হর্টিকালচার উইং এর পরিচালক মো. মিজানুর রহমান। সেমিনারে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
|
|
|
|

রাজধানী ঢাকায় ছড়িয়ে পড়েছে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে আসা জায়ান্ট মিলিবাগ। ইতোমধ্যে এখানকার অনেক ম্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ ভবন চত্বরে দেখা গেছে এদের বেপরোয়া বিচরণ। পরিস্থিতি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ব্যস্ততাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। যেখান থেকেই অভিযোগ পাচ্ছেন সেখানেই ছুটে যাচ্ছেন ডিএই কর্মকর্তারা। জায়ান্ট মিলিবাগ একধরণের ধীর গতির পোকা। যা কাঁঠাল, আম, পেঁপে, লিচু, কলা, পেয়ারা, কুল, লেবু, বেগুণ, শসা, টমোটো, বাঁধাকপি, রেইন্ট্রি ও বাঁশসহ বিভিন্ন গাছপালার রস চুষে খায়। পোকাটি আমের জন্য ভয়ংকর। এটি মানুষকে আক্রমণ এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতি না করলেও সংবেদনশীল মানুষের শরীরে লাগলে চুলকানি হতে পারে।
তবে দলে দলে এদের বিচরন অনেক সময় কমলমতি মানুষের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হোমপ্টেরা বর্গের মনোফ্লেবিডি পরিবারের ড্রসিকা ম্যানজিফেরি নামের এ পোকার জীবন চক্রে ৩টি পর্যায় বিদ্যমান। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু করে জানুয়ারী মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত ডিম ফুটে বাচ্চা বা নিম্ফ বের হয়ে গাছকে আক্রমণ করে। এরা গাছের কচি কান্ড, পাতা, ফুলের কুড়ি, ফুল ও ফল হতে রস চুষে খায় এবং বড় হতে থাকে। তারপর ০৩ বার খোলস বদলায়ে পূর্ণাঙ্গ পোকায় পরিণত হয়। পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী পোকার পাখা নেই, শরীর সাদা পাউডার জাতীয় পদার্থে জড়ানো থাকে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সাদা পাউডারের পরিমাণ বাড়তে থাকে। পূরুষ পোকা লাল বর্ণের এবং এর দুই জোড়া পাখা থাকে। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে স্ত্রী পোকা ডিম পাড়ার জন্য গাছ থেকে নেমে আসে মাটিতে এবং আবর্জনার নীচেয় মাটিতে ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার সময় এরা একধরণের সাদা থলি তৈরী করে। এই থলির ভিতরেই স্ত্রী পোকা ২০০ থেকে ৬০০টি ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার পর স্ত্রী পোকাটি মারা যায়। ডিম তাতক্ষণিকভাবে না ফুটে মাটির নীচেয় সুপ্তাবস্থায় পরবর্তী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত থাকে। এই ডিম পীঁপড়ার মাধ্যমে এবং বর্ষার পানিতে এবং অন্য কোনোভাবে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে থাকে।
ডিএই সুত্রে জানা যায়, ২০১১ সাল থেকে এই পোকা বিমান বাহিনী ঘাটিসহ ঢাকার মহানগরের বহু প্রতিষ্ঠান ও বাড়িতে এই জায়ান্ট মিলিবাগ দমন করা হয়েছে। বিদেশের বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে চলাচলে ব্যবহৃত মটর যানের মাধ্যমে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে পোকাটি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় এসেছে বলে ধারণা করা হয়। ঢাকা এবং ঢাকার আশপাশ ছাড়া এ পোকা এখনো দেশের অন্য কোথাও দেখা যায়নি। এ বছর শের ই বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ফার্মগেট, আসাদ গেটের আশপাশ, আগারগাঁও, জাতীয় সংসদের আশপাশ এবং কলেজ রোডের আশপাশের ভবন চত্বরের বাগানের বহু গাছে এই পোকার দেখা মিলেছে। পোকার বিচরণের সত্যতা স্বীকার করে বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের উপ প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মো. নূরুল ইসলাম বলেন, ডাইমোথোয়েড, ক্লোরোপইরিফস, ইমিডাক্লোপ্রিড ও সাবান পানি একসঙ্গে মিশিয়ে পরপর ২বা ৭দিন পরপর স্প্রে করলে এ পোকা দমন করা যায়। তবে সমন্বিতভাবে ঢাকার সব এলাকায় এক সঙ্গে ম্প্রে করা ছাড়া এপোকা সমূলে দমন হবেনা।
|
|
|
|

দেশের খাদ্যশস্য ভান্ডার হিসাবে খ্যাত চলনবিল অধ্যূষিত তাড়াশ উপজেলায় ইরি-বোরো চাষাবাদের ভরা মৌসুমে ভূ-গর্ভস্থ্য পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন কৃষকরা। গভীর নলকুপ (শ্যালো ) গুলোতে সেচের আশানুরুপ পানি না পেয়ে ১০-১৫ ফুট গর্তে নলকূপ বসিয়ে পানি তোলার চেষ্টা করছেন কৃষকরা।
সরেজমিনে দেখা গেছে, তাড়াশ উপজেলার আটটি ইউনিয়নে ইউনিয়নে গভীর নলকূপের পানি সেচ এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে । ১০ ফুট থেকে ১৫ ফুট পর্যন্ত মাটি গর্ত করে সেচযন্ত্র বসিয়ে পানি তোলার প্রাণান্তর চেষ্টা করছেন কৃষক। আটটি ইউনিয়নের মধ্যে নওগাঁ, মাগুড়া বিনোদ ও সগুনা ইউনিয়নে এ সমস্যা সবচেয়ে বেশি আকার ধারণ করেছে। বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠেই নয়, এ তিনটি ইউনিয়নের বেশিরভাগ সেচ যন্ত্র ( শ্যালো ) দিয়ে সামান্য পানি উঠছে । অনেকেই বাড়ির আঙিনা থেকে ১৫-২০ ফুট নিচে গভীর নলকূপ বসিয়ে পানি তোলার চেষ্টা করছেন।
কৃষক মাগুড়া ও নওগাঁ ইউনিয়নের কৃষক আজগর আলী, রহিচ উদ্দিন, জমশের প্রামানিক, আতাহার হোসেন, চান মিঞাসহ অনেকে জানান, ১০০-১২০ ফুট গভীরে পাইপ বসিয়ে ঠিকঠাক মত পানি পাচ্ছেন না তারা। প্রতি বছরই আশঙ্কা জনকহারে ভূ-গর্ভস্থ্য পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। ১৫-২০ বছর আগেও ৭০-৮০ ফুট মাটির নিচ থেকে এসব এলাকায় বেশ পানি পাওয়া যেত।
তারা আরো জানান, সেচযন্ত্রে পানি কম ওঠায় ইরি-বোরো চাষাবাদে তাদের জ্বালানি খরচ বেড়ে যাচ্ছে । প্রতি মৌসুমে ১ বিঘা জমিতে পূর্বে ১৫-১৬ লিটার জ্বালানি তেল খরচ হলেও বর্তমান সময়ে তা ২৪-২৮ লিটারে গড়িয়েছে। আগের তুলনায় সময়ও লাগছে বেশি। আর বসতবাড়িতে পানি সমস্যায় প্রতিবছরই তাদের নলকূপ আলাদা-আলাদা স্থানে স্থাপন করে পানি সংগ্রহ করতে হচ্ছে।
এ প্রসঙ্গে তাড়াশ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. সাইফুল ইসলাম জানান, চলনবিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ১৬টি নদী মৃত প্রায়। অসময়ে শুকিয়ে যাচ্ছে ডোবা-নালা ও খাল-বিল । ভূ-গর্ভস্থ্য পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় কৃষকের সেচ কাজে সমস্যাটি সাম্প্রতিক সময়ে বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে।
|
|
|
|
|
লাভের আশায় আলু চাষ করে দাম না পেয়ে বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়েছেন রংপুর অঞ্চলের কয়েক লাখ কৃষক।
রংপুর অঞ্চলে আলু চাষ করতে এবার বীজ, সার, কীটনাশক ও মজুরি মিলিয়ে একর প্রতি খরচ হয়েছে এক লাখ টাকা। আর সেই জমির আলু বিক্রি করতে হচ্ছে মাত্র পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকায়।
অর্থনীতিবিদদের মতে কৃষকের লোকসান পুষিয়ে দিতে আলু রপ্তানিসহ কৃষিভিত্তিক শিল্প স্হাপনে গুরুত্ব দিতে হবে। আর কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বলছে, ভালো দাম পেতে হলে আলু সংরক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে কৃষককে।
এ বছর রংপুর অঞ্চলে গ্রানুলা, কার্ডিনাল, ডায়মন্ডসহ বিভিন্ন জাতের আলু চাষ হয়েছে ৯৪ হাজার ৮৪৩ হেক্টর জমিতে। এরই মধ্যে ৯২ ভাগ জমির আলু তোলা হয়েছে।
|
|
|
|

বরগুনার পাথরঘাটার বাজার গুলোতে প্রচুর ইলিশের দেখা মিলছে। সাধারণত এ সময়ে বাজারে তেমন ইলিশ থাকে না। যা পাওয়া যায়, সেগুলো হিমাগারের। তবে এখন ইলিশের ছড়াছড়ি দেখে অবাক ক্রেতারা। দামেও তুলনামূলক কম।
৫০০ গ্রামের কম ওজনের ছোট ইলিশ প্রতি কেজি ২৫০ থেকে ৩০০ টাকায় বিক্রি হয়, যা আগের ছিল ৫০০ টাকা। এর চেয়ে বড় ইলিশ আকারভেদে প্রতিটি ১০০ থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত দাম কমেছে। ৫০০ থেকে ৬০০ গ্রাম ওজনের প্রতিটি ইলিশ বেচাকেনা হয়েছে ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকায়। ৭০০ থেকে ৮০০ গ্রাম ওজনের প্রতিটি ইলিশ মিলেছে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকায়। ৯০০ গ্রামের কমবেশি ওজনের ইলিশ মিলেছে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকায়। এক কেজি ওজনের ইলিশ হাজার টাকায় বিক্রি হয়।
বাজারের আবাসিক এলাকা ও অলিগলিতে ভ্যানে ও হাঁড়িতে করে ইলিশ বিক্রি শুরু হয়েছে আবার। যদিও এখন ইলিশের ভরা মৌসুম নয়।
জানা যায়, প্রতিবছর মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ইলিশ ধরার মৌসুম। এর পরে নদীর পানি কমে যায়। ফলে উজানের স্রোত না থাকায় নদী ও সমুদ্রে তেমন ইলিশ ধরা পড়ে না। কিন্তু এবার ঘটেছে ব্যতিক্রম। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ ধরা পড়েছে। অসময়ে এত ইলিশ ধরা পড়ায় তা সারা দেশের বাজারগুলোতে যাচ্ছে। ফলে মৌসুম ছাড়াও অসময়ে তাজা ইলিশ খাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন ক্রেতারা।
|
|
|
|

মোঃ রহমত আলী :
সোনালী আঁশ খ্যাত পাট জাত ফসল হবিগঞ্জ থেকে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবার (৬ মার্চ) ছিল জাতীয় পাট দিবস। পাট ও বস্ত্র মন্ত্রনালয়ের অধিনে সারাদেশের ন্যায় হবিগঞ্জেও দিবসটি পালিত হয়েছে। কিন্তু যারা এটি আবাদ করে সোনালী আঁশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাদের কতজন জানেন উক্ত দিবসের কথা, এর কোন একটা হিসেব হয়তো কেউ দেখাতে পারবেন না। হবিগঞ্জ কৃষিসম্প্রসারণ বিভাগের এক কর্মকর্তা জানন, অতীতে বাংলাদেশে ব্যপক হারে পাট চাষ হতো। পাট বিদেশে রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা হতো। তখন অধিক মুনাফা হয়ায় কৃষকদের মাঝে পাট চাষে আগ্র ছিল বেশি। প্রযুক্তির আড়ালে উদ্ভাবিত বিভন্ন পণ্য বাজারে পর্যাপ্ত পরিমানে থাকায় পাট ও পাটের তৈরী প্রণ্যর চাহিদা কমে যায়। ফলে বিক্রি করার কঠিন জামেলায় জড়িয়ে পাট বিপনন কাজে এগিয়ে আসতে চায় না কেউ। ফলে পাট চাষে পিছিয়ে পড়েছে হবিগঞ্জের কৃষক। তিনি বলেন, যদি পাটের অধিকতর মূল্য পাওয়ার সুযোগ কৃষকদের হয় তাহলে আবারও পাট চাষে এগিয়ে আসবে তারা। ফলে হারিয়ে যাওয় পাটের সোনালী দিনগুলে ফোটে উঠবে স্বরবে। তাছাড়া প্লাষ্টিক জাতিয় নানা বস্তুও বাজারে সমাগম থাকায় পাটের রশি, ব্যাগ, বস্তা, কার্পেটসহ পাটের তৈরী অনান্য পণ্যে চাহিদাও তেমন একটা নাই।
কৃষি বিভাগ সূত্রে জানাযায়, চলতি মওসুমে জেলার মাধবপুর, লাখাই ও বানিয়াচং উপজেলায় মাত্র ৪শ ৮৫ হেক্টর জায়গায় পাট চাষ করেছেন কৃষক। সূত্র জানায়, পাট উৎপাদন নয় পাটকে সবজির জন্য এখন অনেকাংশে আবাদ করছে চাষীরা।
|
|
|
|
|
কুষ্টিয়া খোকসা উপজেলা মৎস অফিসের আয়োজনে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাজস্ব অধীনে উপজেলার মৎস চাষীদের চিংড়ি চাষের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কু্ষ্টিয়া জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ গোলাম কিবরিয়া। খোকসা উপজেলা মৎস্য অফিস কর্তৃক আয়োজিত উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে চিহ্নিত ২০ জন মৎস্য খামারীগণ ও মৎস চাষিগণ প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণ করেন। সকাল ১০ টা থেকে দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণের উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা খন্দকার সহিদুর রহমান উপজেলার চিংড়ি মৎস্য খামারের বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ব্যবস্থাপনায় চিংড়ি চাষ আরো সহজলভ্য করতে বিভিন্ন কলাকৌশল ও বৈজ্ঞানিক দিক নির্দেশনামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন । উপজেলায় চিংড়ি চাষে মৎস্য চাষীদের উদ্বোদ্ধ ও সুসংগঠিত করতেই এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে বলে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জানান। উক্ত পশিক্ষণ অনুষ্ঠানের উপজেলা মৎস্য অফিসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন
|
|
|
|
|
চলনবিলে এ বছর সরিষার বাম্পার ফলন হয়েছে । চলনবিলের ৯টি উপজেলার এছর প্রায় ৪৫ হাজার হেকক্টর জমিতে সরিষার চাষাবাদ করা হয়েছে । তাড়াশ উপজেলা কৃষি অফিসসূত্রে জানা যায় চলতিবছর এই উপজেলায় প্রায় ৫ হাজার ২শত হেক্ট্রর জমিতে সরিষার চাষ করা হয়েছে ।
সরজমিনে উপজেলার কুন্দইল ,মাকড়শোন ও কামারশোন গ্রামের মাঠে গিয়ে দেখা যায় কৃষকরা সরিষার তুলছেন ।
মাকড়শোন গ্রামের কৃষক আবু সাইদ জানান, সরিষার ফলন ভাল হয়েছে এবং দাম ও ভাল রয়েছে ।
কুন্দইল গ্রামের কৃষক আজিজুল ইসলাম জানান, বিঘা প্রতি ৮-১০ মনহারে ফলন হচ্ছে ফলে কৃষকরা খুশি ।
তাড়াশ উপজেলা কৃষি অফিসার সাইফুল ইসলাম জানান, সরিষার জন্য আবহাওয়া অনুকুলে ছিল ফলে সরিষার বাম্পার ফলন হয়েছে ।
|
|
|
|

কৃষকরা সেই ধান কেটে আঁঁটি বেঁধে সিড়িঁর মতো করে সাজিয়ে রাখতো। আর সেখান থেকেই নদীর নাম ধানসিঁড়ি। স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিরা বলেন, সেসময় বিশাল এ নদীতে সুপারির হাট বসতো। নদীপথেই মাইলের পর মাইল ছেয়ে যেত হাজার হাজার নৌকায়। দক্ষিণাঞ্চলের সবচেয়ে বড় সুপারির হাট বসতো ধানসিঁড়ি নদীতে। এই নদীর সঙ্গে কবি জীবনানন্দের মিতালী যেন এক জন্মে শেষ হওয়ার নয়, তাই তো তিনি আবারো ফিরে আসতে চেয়েছেন এই ধানসিঁড়িটির তীরে।
‘হায় চিল /সোনালি ডানায় চিল/ এই ভিজে মেঘের দুপুরে/ তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে।’ জীবনানন্দের সোনালি ডানার চিল কিংবা বুনোহাঁস, শালিক অথবা ভোরের কাক আজো আছে। কিন্তু কবিতার সেই কালজয়ী ধানসিঁড়ি আজ মরে যাচ্ছে। এককালের জাহাজ চলা নদীটি আজ নাব্যতা হারিয়ে স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়ার পথে। মৃত্যুর পরেও কবি যে নদীটির তীরে ফিরে আসতে চেয়েছেন (আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে, এই বাংলায়, হয়তো মানুষ নয় শঙ্খচিল শালিকের বেশে...) সে নদীটি হারিয়ে যাওয়ার তীব্র বেদনায় কবির সেই সোনালি ডানায় চিলগুলো যেন কেঁদে মরছে।
ঝালকাঠির সুগন্ধা, বিশখালি আর সুয়েজ খাল গবাখন চ্যানেলের মোহনা থেকে কবিতার সেই ধানসিঁড়ি নদীটি প্রবাহিত হয়েছে। এরপর ঝালকাঠি সদর উপজেলার ধানসিঁড়ি ইউনিয়নের মধ্য থেকে প্রবাহিত হয়ে নদীর অপরপ্রান্ত গিয়ে বাগড়ি বাজারের তীরবর্তী জাঙ্গালিয়া নদীতে পড়েছে। জনশ্রুতি রয়েছে, এককালে নদীটি এমন প্রশস্থ ছিল যে, এক ডোঙা ধান সিদ্ধের জন্য যতক্ষণ সময় লাগতো, নদী পার হতেও ততোক্ষণ সময় লাগতো। তাই সেসময় নদীটিকে ধান সিদ্ধের বাঁকও বলা হতো। আবার কারো কারো মতে, এ নদীর বিশাল চরে আগে ধান চাষ হতো। কৃষকরা সেই ধান কেটে আঁঁটি বেঁধে সিঁড়ির মতো করে সাজিয়ে রাখতো। আর সেখান থেকেই নদীর নাম ধানসিঁড়ি। স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিরা বলেন, সেসময় বিশাল এ নদীতে সুপারির হাট বসতো। নদীপথেই মাইলের পর মাইল ছেয়ে যেত হাজার হাজার নৌকায়। দক্ষিণাঞ্চলের সবচেয়ে বড় সুপারির হাট বসতো ধানসিঁড়ি নদীতে। আর এ নদী দিয়েই ভেঁপু (স্টমারের সাইরেন) বাঁজিয়ে বড় বড় সব স্টিমার যেত খুলনাসহ দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে।
ঝালকাঠির রাজাপুরে স্থানীয়ভাবে কবি জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে গবেষণা করা অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক সোহরাব হোসেন বলেন, ‘বরিশাল ব্রজমোহন স্কুল শিক্ষক ও ‘ব্রহ্মবাদী’ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রবন্ধকার সত্যানন্দ দাশ এবং নারী কবি কুশুম কুমারী দাশের ছেলে জীবনানন্দ ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার বামনকাঠি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের ১০ বছর পর বাবার শিক্ষকতার সুবাদে বরিশালে বসবাস শুরু করে কবি পরিবার। এরপর বেড়ে ওঠা শিক্ষাজীবন সবই বরিশালে। কবির পৈত্রিক বাস ছিল বিক্রমপুর জেলায়। নদী ভাঙনের কারণে কবির জন্মের আগেই তারা ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার বামনকাঠিতে চলে আসেন। কবি মাতা নারী কবি কুসুম কুমারী দাশ জন্ম একই গ্রামে। সে আত্মীয়তার সুবাদেই কবি পিতা স্বপরিবারে ঝালকাঠি চলে আসেন। জমি কিনে বামনকাঠি গ্রামে বসবাস শুরু করেন। পরে কবি পিতা বরিশালে বসবাস শুরু করলেও কবির চাচার পরিবার বামনকাঠিতেই ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বসবাস করেন। কবি পরিবার বরিশাল থেকে গ্রামে আসা যাওয়া করতেন নানা উত্সব আয়োজনে। সেসময় কলতাকার লেখক-কবিদের নিয়েও নানা উত্সব বসতো ঝালকাঠির ওই গ্রামে।
যদিও বই-পুস্তকে কবির জন্মস্থান বরিশালে উল্লেখ করা হয়েছে।’ কেবল ঝালকাঠির গবেষক শিক্ষক সোহবার হোসেনই নয়, গত কয়েকবছর ধরে দেশের অনেক কবি-লেখকই ঝালকাঠির বামনকাঠি গ্রামকেই কবির জন্মস্থান দাবি করে আসছেন। এদিকে, এক সময় একমাত্র নদীপথ ধানসিঁড়ি হয়েই বারবার কবি ঝালকাঠি আসেন নিজবাড়ি কিংবা মামা বাড়িতে। সেই সুবাদেই ধানসিঁড়ি নদীটির রূপ ছুঁয়ে যায় তার কবিতায় বারবার। কবির বিখ্যাত ও সুপরিচিত কবিতা ‘আবার আসিব ফিরে’ ছাড়াও ধানসিঁড়ির নৈসর্গিক রূপ কিংবা চির সত্য মৃত্যুকে কবি তুলে ধরেছেন এভাবেই ‘একদিন জলসিঁড়ি নদীটির পাড়ে এই বাংলার মাঠে বিশীর্ণ বটের নিচে শুয়ে রব, পশমের মত লাল ফল ঝরিবে বিজন ঘাসে, বাঁকা চাঁদ জেগে রবে, নদীটির জল বাঙালির মেয়ের মত বিশালাক্ষী মন্দিরে ধূসর কপাটে।’ আবার আসিব ফিরে কবিতার আরেক পংক্তিতে ধানসিঁড়ি নদীর শাখা রূপসা খালটি উঠে এসেছে কবিতার চরণে এভাবে ‘রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে/ ডিঙ্গা বায়; রাঙ্গা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে।’ ভৌগলিকভাবে যারা ঝালকাঠির এ রূপসা খালটিকে চিনবেন না তারা হয়তো মনে করবেন, কবি খুলনার রূপসা নদীর কথা বলেছেন। ঝালকাঠির এ রূপসা খালটি ধানসিঁড়ি নদীর একটি শাখা খাল। ঝালকাঠির গাবখান ব্রিজ থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে বৈদারাপুর গ্রামের ভেতর থেকে চলে গেছে খালটি। কবির গ্রাম বামনকাঠি থেকে তত্কালীন ধানসিঁড়ি নদীতে নৌকায় কবিও যৌবন কিংবা কৈশোরে ঘুরে বেড়িয়েছেন অনেকবার। রূপসার সাদা ছেঁড়া পালে ডিঙ্গা বাওয়া কিশোরটি হয়তো কবি নিজেই। আর সেই রূপেই মৃত্যুর পরে কবি আরো ফিরে আসতে চেয়েছেন ধানসিঁড়ির তীরে।
কবির হায়চিল কবিতায়্ত‘হায়চিল সোনালি ডানার চিল/ এই ভিজে মেঘের দুপুরে তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানর্সিড়ি নদীটির পাশে/ তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মত তার ম্লান চোখ মনে আসে/ পৃথিবীর রাঙা রাজ কন্যাদের মত সেজে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে/ আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হূদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!’ কবিতার সোনালি ডানায় চিলেরা আজো কেঁদে মরে। তবে এ কান্না ধানসিঁড়ি নদীটির অস্তিত্ব হারিয়ে বিলিন হতে চলার বেদনায়। এককালের জাহাজ চলা নদীতে আজ যেন নৌকা চলতে ও বাঁধা পায়। নাব্যতা হারিয়ে নদীটি এখন সর্বোচ্চ গভীরতায় ৫ ফুট আর চওড়ায় ৭ ফুটের বেশি নয়। তাই ধান সিদ্ধের বাঁকের কাহিনি আজ আষাঢ়ে গল্পের মতো। এভাবেই আরো কিছুদিন কাটলে হয়তো নদীটির অস্তিত্ব কেবল বইয়ের পাতাতেই থাকবে। স্থানীয়রা জানায়, গাবখান সেতুর পূর্ব ঢাল থেকে দক্ষিণ দিকে উত্স মুখ পর্যন্ত নদীর চরে লোকজন এখন ধান চাষ করেছে। আর সেতু থেকে পূর্বদিকে রবি শষ্য চাষ করা হয়। রাজাপুর উপজেলার পিংড়ি থেকে ধানসিঁড়ি গ্রামে নদীর মিলিত স্থান পর্যন্ত পিংড়ি সেতুর দু-পাশে প্রায় ১ কিলোমিটারজুড়ে ছোট-বড় অসংখ্য চর। উত্স মুখ খনন না করেই এর প্রায় সাড়ে ৩ কিলোমিটার ভাটিতে নাব্যতার জন্য প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ে খনন কাজ করা হয়েছে ২০১১ সালে। আর তারপর কেটে গেছে আরো কয়েকবছর। পলি পড়তে পড়তে নদীর নব্যতা একেবারেই হারাতে বসেছে। তবে এখনো বিভিন্ন সময় অনেক পর্যটক আসেন কবিতার সেই ধানসিঁড়ি দেখতে। এমনকি কলকাতা থেকেও কবি কিংবা সাধারণ পর্যটকও আসেন। তবে যতটা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তারা আসেন, নদী দেখে ততোটাই হতাশ হন। তবুও ঐতিহ্য রক্ষার লড়াইয়ে কোনোমতে বয়ে চলা এই ধানসিঁড়ি নদীতে আজো পড়ন্ত বেলায় সূযের্র খেলা চলে। ভিজে মেঘের দুপুরে সোনালি ডানায় এখনো চিল উড়ে বেড়ায়। আর নদীর দু-ধারে গড়ে ওঠা বেড়ি বাঁধে সারি সারি গাছের ছায়ায় দীর্ঘ মেঠোপথ পর্যটকদের কিছুটা হলেও মন কাড়ছে। সরকারিভাবে উদ্যোগ নিলে কবি জীবনানন্দের স্মৃতি রক্ষায় নদীটি যথাযথ খনন করে পুরোনো ঐতিহ্য অনেকটা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তাহলে হয়তো জীবনানন্দের কালজয়ী কবিতার ধানসিঁড়ি নদীটি বেঁচে থাকবে জীবন্ত বাস্তবে।
|
|
|
|

নাটোর: নাটোরের কৃষকরা বোরো ধান আবাদে এখন ব্যস্ত সময় অতিক্রম করছেন। চলতি রবি মৌসুমে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কাছাকাছি থাকা বর্তমানে আবাদ কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। আবাদি জমির পরিধি লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করার পাশাপাশি ফলনের সম্ভাবনাও রয়েছে আশাতীত।
জেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ সূত্রে জানা যায়, চলতি মৌসুমে জেলায় মোট ৫৫ হাজার ৪০১ হেক্টর জমিতে বোরো ধান আবাদের মাধ্যমে দুই লাখ ১৮ হাজার ১৮৩ টন চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
ইতোমধ্যে জেলার সাতটি উপজেলায় মোট ৫৩ হাজার ৯০৫ হেক্টরে আবাদ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। এরমধ্যে উচ্চ ফলনশীল জাতের আবাদি জমির পরিমাণ সর্বাধিক ৫২ হাজার ৮২৩ হেক্টর, হাইব্রিড জাতের চারা রোপন করা হয়েছে মোট ১০ হাজার ৫৭ হেক্টরে এবং ২৫ হেক্টরে স্থানীয় জাত।
চলতি মৌসুমে বরাবরের মতই উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ধান আবাদে কৃষকদের আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এরমধ্যে সরু জাতের জিরাশাইল বা মিনিকেট ধানের আবাদী জমি ২৮ হাজার ৮৪০ হেক্টর।

ব্রিধান-২৮ ও ব্রিধান-২৯ চাষের প্রতিও কৃষকদের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। ব্রিধান-২৯ এ পর্যন্ত আবাদ হয়েছে ১৩ হাজার ৫৭০ হেক্টরে এবং ব্রিধান-২৮ পাঁচ হাজার ৪১৫ হেক্টরে।
নাটোরে জেলায় বোরো ধানের আবাদি জমির অর্ধেকের অধিক জমি চলনবিল অধ্যুষিত শস্য ভান্ডার খ্যাত সিংড়া উপজেলাতে। সিংড়া উপজেলায় ৩৭ হাজার ১০০ হেক্টর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ইতোমধ্যে সাড়ে ৩৫ হাজার হেক্টরে হাষাবাদ হয়েছে বলে আবাদ অগ্রগতির প্রতিবেদনে জানা যায়। এই উপজেলায় আগামী এক সপ্তাহ পর্যন্ত আবাদ কার্যক্রম চলবে এবং লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে অতিরিক্ত এক হাজার হেক্টর জমি চাষাবাদের আওতায় আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সাজ্জাদুল ইসলাম।
কৃষকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে বোরো আবাদে তাঁরা লাইন লোগো পদ্ধতি ব্যবহার করছেন। এছাড়া জমিতে পাখির মাধ্যমে ক্ষতিকর
পোকামাকড় নিধনের জন্যে গাছের ডাল রোপন করে পার্চিং পদ্ধতি অনুসরণ এবং গুটি ইউরিয়ার ব্যবহারও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। লাইন লোগো পদ্ধতিতে ধানের চারা রোপন করলে আগাছা নিধনসহ জমির পরিচর্যা সহজ হয় এবং পার্চিং পদ্ধতি ও গুটি ইউরিয়ার ব্যবহারে ধানের ফলন বৃদ্ধি পায় বলে জানান সিংড়া উপজেলার বড় সাঁঐল গ্রামের কৃষক সাইফুল ইসলাম।
একই এলাকার কৃষক আবুল খায়ের এক সপ্তাহ আগে জমিতে ধানের চারা লাগিয়েছেন। গাছের গোড়ায় গোড়ায় গুটি ইউরিয়া দেওয়ার সময় তিনি বলেন, কৃষি শ্রমিকের খুব সংকট, তাই নিজেই জমিতে কাজ করছি।
নাটোর সদর উপজেলার কাফুরিয়া ইউনিয়নের চাঁদপুর কৃষি ব্লকের উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, এই ব্লকে বেশিরভাগ কৃষক সারি পদ্ধতিতে ধান রোপন করেছেন। লোগো পদ্ধতি অনুসরণ এবং পার্চিং ও গুটি ইউরিয়ার ব্যবহারও দৃশ্যমান অনেক আবাদী জমিতে। উঁচু জমিতে বোরো আবাদ কার্যক্রম শেষ হলেও বন্যা এবং জলাবদ্ধতার কারনে তুলনামূলক নীচু জমির আবাদ কার্যক্রম দেরীতে শুরু হয়েছে বলে জানান মাঠ পর্যায়ের এই কর্মকর্তা।
সিংড়া উপজেলার কুমিরা গ্রামের আদর্শ কৃষক জুলফিকার আনাম তারা চলতি মৌসুমে ১৭ বিঘা জমিতে ঝড়-বৃষ্টি সহনীয় ব্রি-২৮ ও ব্রি-২৯ জাতের ধান চাষ করেছেন।
উৎপাদনের সম্ভাবনা সূচক প্রশ্নের উত্তরে আদর্শ কৃষক তারা বলেন, বিঘা প্রতি গড়ে ৩০ মণ ফলন হবে বলে আশা করছি। সম্ভাব্য উৎপাদনের অন্তত: ৫০০ মণ ধানের সবটুকুই বীজ উৎপাদকের কাছে বিক্রি করবেন বলে অনুকূল আবহাওয়ায় উন্নত ফলনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন এই কৃষক জানান।
নাটোর কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপ পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, চলতি মৌসুমে বন্যার পানি নামতে দেরি হওয়াতে জেলার কৃষকরা বোরো আবাদে অধিক আগ্রহী হয়েছেন বলে আবাদী জমির পরিধি লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পাশাপাশি অনুকূল আবহাওয়া এবং কৃষি বিভাগের পরামর্শে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে ধানের উৎপাদনও হবে উন্নতমানের এবং আশাতীত।
|
|
|
|

চলতি মাসে রয়েছে বসন্ত দিবস, ভালোবাসা দিবস, ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আর তাই এই তিনটি দিবসকে কেন্দ্র করে যশোরের গদখালীর ফুলচাষিরা নিচ্ছে নানা ধরণের প্রস্তুতি। পাশাপাশি ব্যবসায়ীরাও আশা করছে ফুলের ভলো দাম পাওয়ার।
ফুলের রাজধানী যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালী এলাকার ফুল চাষিরা প্রতি মৌসুমে ৭টি উৎসবকে ঘিরে মূল বেচাকেনা করে থাকেন। উৎসবগুলোর মধ্যে স্বাধীনতা দিবস ও ইংরেজি নববর্ষের বেচাকেনা শেষ করেছেন তারা। আর চলতি মাসেই রয়েছে বসন্ত দিবস, ভালোবাসা দিবস, ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং এই তিন উৎসবেই বেশি ফুল বিক্রি করে থাকেন চাষিরা। তাই নানা পদ্ধতিতে মাঠে পর্যাপ্ত ফুল সংরক্ষণ করছেন তারা।
স্থানীয় ফুলের পাইকারি ব্যবসায়ীরা বলেন, এই বছর বাজার ভালো। উৎসবের আগে ফুলের দাম আরও বাড়বে বলে আশা করছি আমরা। আর ওই দিন প্রতিটি গোলাপ বিক্রি হবে ১৩-১৪ টাকা করে।
ফুল চাষীরা বলেন, আমরা উৎসবগুলোকে সামনে রেখে ফুলগুলোকে ক্যাপ পড়িয়ে রেখেছি, যেন ফুলগুলো ফুটে না যায়। পাশাপাশি সার দেওয়াও বন্ধ রেখেছি।
যশোরের বাংলাদেশ ফ্লাওয়ারস সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রহিম বলেন, ফেব্রুয়ারি মাসের তিন উৎসবেই প্রায় ৪০ কোটি টাকার ফুল বিক্রি হবে।
বর্তমানে এলাকার ৬ হাজার কৃষক বাণিজ্যিকভাবে রজনীগন্ধা, গোলাপ, জারবেরা, গাঁদা, গ্লাডিউলাস, জিপসি, রডস্টিক, কেলেনডোলা, চন্দ্র মল্লিকাসহ ১১ ধরণের ফুল উৎপাদন করছেন।
|
|
|
|

দেশের সাদা সোনা খ্যাত চিংড়িসহ সকল প্রকার মাছ রপ্তানিকে উৎসাহিত করতে অর্থ সহায়তা দেওয়া হবে। এজন্য হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রফতানিতে পাওয়া যাবে নগদ সহায়তা। সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, হিমায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বরফ আচ্ছাদন এবং ব্যবহৃত আনুষঙ্গিক আবশ্যিক উপাদান হিমায়িত মাছের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য হবে।
প্রজ্ঞাপনে আরো বলা হয়, ২০০২ সাল থেকে হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রফতানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। ২০০৩ সালে হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রফতানির ক্ষেত্রে আইকিউএফ রিটেইল প্যাকের সংজ্ঞা, প্যাকেটের সর্বোচ্চ ওজন, ইউনিট প্রতি (পাউন্ড) এফওবি মূল্যের সিলিং, প্রভৃতি বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে হিমায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রফতানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রযোজ্য।
জানা গেছে, হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ রফতানির নগদ সহায়তা প্রদানের জন্য প্রথমে এলসির আওতায় রফতানি মূল্যের ওপর নগদ সহায়তা দেওয়া হয়। এতে মূল্য ঘোষণার ক্ষেত্রে ওভার ইনভয়েসিং করে নগদ সহায়তার অর্থ হাতিয়ে নেয় অসাধু কিছু ব্যবসায়ী। এমন ঘটনার প্রেক্ষাপটে ২০০৩ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি নীতিমালা জারি করে। ওই নীতিমালায় রপ্তানিকৃত মাছে প্রতি ইউনিটির একটি সর্বোচ্চ এফওবি মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়।
|
|
|
|

চাহিদা বাড়লেও দেশে দ্রুত কমছে শক্তিবর্ধক ছোলার আবাদ। ফল ছেদক পোকা ও বোট্রাইটিস গ্রে মোল্ড রোগের প্রকোপ এবং অন্যান্য ফসলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারায় ব্যাপকভাবে কমছে ছোলার আবাদ। উৎপাদন ৮০ হাজার মেট্রিক টন থেকে ৭ হাজার মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে। দেশে অবস্থান হারিয়ে ষষ্ঠ স্থানে নেমে এসেছে। অথচ বারি’র গত জুন মাসের হিসেবে ডাল ফসলের এলাকা ও উৎপাদনের দিক থেকে ছোলা ছিল পঞ্চম। তখন দেশের প্রায় ৮ হাজার হেক্টর জমিতে প্রায় ৯ হাজার মেট্রিক টন ছোলা উৎপাদন হতো প্রায় ৯ হাজার মেট্রিক টন। বর্তমানে ৫ হাজার ৮০০ হেক্টর জমিতে ছোলা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৬৮০০ মেট্রিক টন।
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বারি’র ডাল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. মোহাম্মদ হোসেন বলেন, জীবনকাল ৪ মাসের বেশি হওয়ায় নাজুক দশায় পড়েছে ছোলা। রবি মৌসুমে ছোলার জমির দখল নিচ্ছে অনান্য ফসল। পরিস্থিতি মোকাবেলায় চলতি বছর মার্চ মাসে তাপ খরা ও রোগ প্রতিরোধী বারি ছোলা ১০ অবমুক্ত হয়েছে। আগামী বছর মাঠ পর্যায়ে এই জাতের ছোলার আবাদ হলে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হবে। অপেক্ষাকৃত কম জীবন কালের এই জাতের ছোলা হেক্টরে ১৮০০ থেকে ২০০০ কেজি ফলন দেবে। এ যাবত বারি উদ্ভাবিত ছোলার ১০টি উন্নত জাতের মধ্যে বারি ছোলা-৫ ও বারি ছোলা-৯ উচ্চফলন ও রোগসহনশীল। এছাড়া বারি ছোলা-৮ একমাত্র কাবুলী জাত। ২০১১ সালে বারি ছোলা-৯ এবং ১৯৯৬ সালে বারি ছোলা ৫ অবমুক্ত হয়। ছোলার এ জাতগুলো একক ফসলের পাশাপাশি আন্তঃফসল হিসেবে চাষ করে লাভবান হওয়া যায়।
আবাদ ও উৎপাদনের বেহাল দশার কারণে এবছর অনেক বেশি পারিমাণে ছোলা আমদানি করতে হবে বলে কৃষিবিদদের ধারণা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংগনিরোধ (কোয়ারেন্টাইন) উইং সূত্রে জানা গেছে, বিগত বছরগুলোতে দেশে গড়ে প্রায় ২ লাখ মেট্রিক টন ছোলা ও ছোলার ডাল আমদানি করা হয়।
|
|
|
|
|
|
|